পোস্ট বার দেখা হয়েছে
শিশু রবির মানস জগৎ
অরিজিৎ রায়
(চতুর্থ পর্ব )
এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক। শিশু থেকে বালক বয়সের উত্তরণে কবির মানস জগতকে ছুঁয়ে গেছে বিভিন্ন বিষয় - যা তাঁকে আলোড়িত করেছে, নতুন নতুন বোধের জন্ম দিয়েছে, কবি সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে আর মানুষ চিনতে সাহায্য করেছে। এমন একটি পরিবারে কবির বড় হওয়া যেখানে ইচ্ছা করলেই মানসিক পুষ্টি আহরণের একাধিক অবকাশ ছিল। ছিল না রক্ষণশীলতা, ছিল না অর্থনৈতিক দৈন্যতা, ছিল না কুসংস্কার, ছিল না বিবিধ বিষয়ভিত্তিক বই এবং তথ্যের অপ্রতুলতা। দেশ বিদেশের সমাজ অর্থনীতির সাথে ছিল নিবিড় আদান প্রদান। ভারতীয় সংস্কৃতির এক সুপরিকল্পিত বিবিধ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ ছিল শিশু রবির একান্নবর্তী পরিবার। তাই শিশু থেকে কৈশোর পেরিয়ে বালক বেলা পর্যন্ত কবির বেড়ে ওঠায় পরিবারের এক বিশেষ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। যা তাঁর মানস জগৎ গঠনে একটি সুষ্ঠ ছন্দের অবতারণা ঘটিয়েছিল।
শিশু রবি জন্মসূত্রে যে স্বাদেশিকতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন - " জীবন স্মৃতি" গ্রন্থে তার পরিচয় সূরক্ষিত। সপ্ততি জয়ন্তী উৎসবকালে ছাত্রদের সংবর্ধনার প্রতিভাষণে তিনি তা যেমন সংক্ষেপে স্মরণ করেছেন তেমনই তাঁর রচনাবলীতে 'অবতরণিকা' রূপে সেই প্রতিভাষণ স্থান লাভ করেছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় স্বাদেশিকতার ইতিহাসে সেই পর্বটি ছিল হিন্দুমেলার পর্ব।
কবি লিখেছেন - " হিন্দুমেলার পরামর্শ আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা - 'জয় ভারতের জয়' গুণদাদার লেখা - 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে', বড়দাদার - 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি।' জ্যোতি দাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়া বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগবেদের পুঁথি, মড়ার হাড়ের খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।" (রচনাবলী ১ম - পৃ:১৯০)
অবশ্য এই প্রকার 'ক্ষাপামির তপ্ত হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো' ছিল রবির স্বভাব বিরুদ্ধ। তবু স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ ছিল অপরিসীম, ঠাকুর পরিবারে খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্বাদেশিকতার প্রতি আকর্ষ ছিল প্রবল। স্বদেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, স্বদেশীয় বেশভূষা চাল - চলনের প্রতি আকর্ষণ! মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, এসব তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকার। তেরো বছরের বালক রবি, কবি রূপে ' দিল্লি দরবার' সম্বন্ধীয় স্বদেশী কবিতাও সেখানেই পাঠ করেন(ইং ১৮৭৭)। এ কালের ভাষায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি 'কমিটেড' বা 'স্বদেশীয়' কবি ।
সে সময় অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে ঠাকুর পরিবারে সামাজিক হাওয়াও বইছিল। কিন্তু নতুন ও পুরাতনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতায় দুই-ই ছিল সম্মিলিত। এ মেলার দু-একটি বৈশিষ্ট্য তাই স্মরণীয়। প্রথম কথা, হিন্দুমেলা নামটি থেকেই সহজবোধ্য - রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ উদ্যোক্তাদের কাছে "হিন্দু" ও "ন্যাশনাল" ছিল সমার্থক, আর "ভারতবর্ষীয়ত্ব" অর্থ "হিন্দুত্ব" ; দ্বিতীয় লক্ষণীয় হিন্দু মেলার কর্মকাণ্ড। তা মূলতঃ গঠনমূলক, এবং মোটেই "রাজনৈতিক" নয়। আজ ২০২১ এ দাঁড়িয়ে ২০১৪ উত্তরকালে ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতিতে যেভাবে উগ্র হিন্দুত্ব মাথা চাড়া দিয়েছে বা যে মেকী দেশ-প্রেমের উদ্ভাবন ঘটেছে এবং মেকী হিন্দুত্ববাদ (এক কথায় মুসলমান ঘৃণা ও বিদ্বেষ) যেভাবে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে হানা দিচ্ছে ঠিক তেমনটা ছিল না ঐ হিন্দুমেলা। সেখানে মুসলমান বিরোধিতা ছিল না বা এখনকার মতো হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না। তাই তো কবি লিখতে পেরেছিলেন - "পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ / বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ"
অথবা
"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-
/ শক-হূন-দল-পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।" ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় ভারতীয় ধারার সংগঠনের (মেলা) মধ্য দিয়ে দেশের সম্মুখে উপস্থিত করাই ছিল হিন্দু মেলার প্রধান কাজ। স্বাদেশিকতার এই দুই ঐতিহ্যই রবীন্দ্রনাথ বালক বয়স থেকেই তাঁর পরিবার - পরিবেশ থেকে লাভ করেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় যে স্বাদেশিক মতাদর্শ ক্রমে গড়ে ওঠে, পরিবর্তন - পরম্পরার মধ্য দিয়ে সেই উত্তরাধিকার যে একেবারে লক্ষ্য না করা যায় তা নয় - এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।
রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাঁর জীবনদর্শনেরই অঙ্গ, তাঁর দ্বারা বিশিষ্ট। সেই জীবনদর্শনের প্রধান কথা তাঁর বিশিষ্ট প্রগতিবাদিতা, অর্থাৎ গতিবাদ (ডায়নামিজম) ও সুষমাবাদ (হার্মনি) মূলক এক ধরণের দ্বন্দ্ব - সমন্বয়ের বিশ্বাস। আরো অনেক সূত্র বা সূক্ষ্ম তত্ত্বও নির্দেশ করা যায়। কারণ, রবি কবির জীবনদর্শনকে এক কথায় মানবতা বা 'মানুষের ধর্ম' বললেও মিথ্যা বলা হবে না। আমাদের পক্ষে যা প্রথম স্মরণীয় তা এই যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন অখণ্ড জীবনদর্শন ; তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিরই তা ফল। এই অখণ্ড দৃষ্টিতে ও মানবতার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় স্বাদেশিকতাকে স্বীকার ও বিচার করেছেন - স্বাদেশিকতার ধর্মসম্মত, যুক্তিসম্মত ও ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসম্মত বিকাশ ছিল তাঁর কামনা ও সাধনা। অবশ্য সেই বিকাশই রবীন্দ্রনাথের নিকট বিকাশ বলে গ্রাহ্য - যে বিকাশ প্রাণবান, যা সৃষ্টি। রবীন্দ্রপ্রতিভা সৃষ্টিধর্মী, তাই স্বাদেশিকতার যে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে সংহত ও রূপায়িত হতে চাইত না, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় তা যথার্থ বিকাশ নয়, সুস্থ ও সার্থক দেশানুরাগও নয়।
এই পরিবার-পরিবেশে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাতে স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর আজন্ম সংস্কার। আর ইতিহাসের যে পর্বে তাঁর জীবন উদযাপিত তাতে মানুষের ভবিতব্য হয়ে উঠেছিল তাঁর সুগভীর ধ্যানের বিষয়। এই জন্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় ও মিথ্যা নয় - তিনি তাঁর স্বদেশের "গ্রেট সেন্টিনেল", বা মহাপ্রতিহার, তিনি আন্তর্জাতিক মৈত্রী - চেতনার অগ্রদূত।
রবি কবির কৈশোরকালে তাঁর পরিবার থেকে কবি যে মানবিক শিক্ষা পেয়েছিলেন তা ছিল কবির সারাজীবনের পাথেয়। যে কোন মানুষের বাল্যকালই গড়ে দেয় তার সারা জীবনের চরিত্র। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানবিক মূল্যবোধ ছিল কবির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সদ্য যৌবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কবি শিলাইদহ থেকে লিখছেন (ছিন্নপত্র - শিলাইদহ । ২০ শে আশ্বিন ১২৯৮) - " উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিন্দ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছাচারিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে।পৃথিবী যে সৃষ্টি কর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ - তা মনে না করে, একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথার্থ দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।" রবির এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি কতটা - মানবিক মূল্যবোধ সম্বলিত, দৃঢ়চেতা এবং বাস্তবধর্মী একজন মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর অন্যতম মূল্যবোধ। মানবতাই যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অন্যতম উৎস তা তিনি বরাবর তাঁর লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
" মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"
( কবিতা 'প্রাণ', কড়ি ও কোমল ১২৯৩)।
রবি কবির বাল্য বয়স থেকে যৌবনের শুরুর মধ্যের দিনগুলিতে যদি ওনার কাব্যের দিকে তাকানো যায়, তবে দেখব "কড়ি ও কোমল" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রয়াসে যে
খঞ্জতা, তার মূলে কবির কল্পনার অপ্রস্তুতি। তখনও পর্যন্ত কবির ভাবাবেগ তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তৃত সমর্থনে পুষ্ট হতে পারেনি। "সোনার তরীর" আগে রবীন্দ্র জীবন সেই সচল অভিজ্ঞতার আভাস মাঝে মাঝে লাভ করলেও, তাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন তিনি "সোনার তরী" - "ছিন্নপত্রের" কালে। এখানে কবি স্বাধীন।
১২৯৮ সালে শিলাইদহ যাত্রার বোট থেকে রচিত হল - "সোনার তরী" -
"একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা -
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া-মসী- মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা --
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।। "
অথবা
" ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই - ছোটো সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে,
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি --
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।।"
সোনার তরী কাব্যগ্রন্থটি সে বিচারে কবির তৎকালীন অভিজ্ঞতার শুদ্ধ দান। এখানে প্রকৃতি চেতনা কখনও নগর জীবনের নেতিতে কল্পিত হয়নি। জীবনের দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করার মুকুর হিসেবে রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহার। বলা যায় তিনি জগৎ ও জীবনের প্রাণস্পন্দনকে প্রতিষ্ঠা করতেন বলেই প্রকৃতির শত শত প্রতিমা গড়ে তুলেছেন। সোনারতরী কবিতাটি যে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল জুড়ে বাঙালি পাঠককে কাব্য-রসামৃত দান করে চলেছে তার মূল এইখানে। কেন কবিতাটি আমাদের শান্তি ও আনন্দ দান করে বা কিসে ঘটে চিত্তলোকের গভীর বিস্তৃতি ? - তাকে খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে, সেই শক্তির উৎস এই কবিতার রূপক নির্মাণের সাহসিক অভিনবত্বে। ধানের খেত, কৃষক ও বর্ষার আকাশ - এই সবকিছুর মিলনের ভিতরে লৌকিক কর্মচঞ্চল জীবনের যে প্রসাদ বিদ্যমান এই কবিতার অন্তরশায়ী কল্পনার পক্ষে তা অলৌকিক স্পর্শের সরূপ। রূপকের এই বিশিষ্টতায় কবিতাটি বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ কবিরা তাদের কল্পনাকে অভিজ্ঞতার সম্পদে করে তোলেন পরম যথার্থ। যে মূল্যে ধৃত হলে সেই পরম প্রসন্নতা লাভ হয়, কাব্যের সম্পদ তারই অভিব্যক্তিকে খুঁজি আমরা কাব্যের আত্মায় ও টেকনিকে। এখানে দেশজ, প্রাকৃত জীবনশ্রয়ী অভিজ্ঞতা কবি কল্পনাকে সজীব করেছিল বলেই এর অবয়বে এসেছে এক গাঢ় বদ্ধ চিত্রল সংহতি। কবিতাটি রবীন্দ্র-কাব্য পর্যায়ে গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ। সোনার ধানের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই স্মৃতি রবীন্দ্র - মানসের সমগ্রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ কল্পনায় স্বর্ণবর্ণ স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসেবে আকৃষ্ট হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমনভাবে কাব্যে ধৃত হল এবং কাব্য - ধৃত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কেমন করে পরবর্তী কাব্য সৃষ্টিকে প্রভাবিত করল সে ব্যাপার এই কবিতাটি তার একটা নিদর্শনও বটে।
সে সময় কবির বয়স তখন ষোলো। জ্যোতিদাদা তাদের বড়দাকে সম্পাদক মনোনীত করে ভারতী পত্রিকা বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম বছরে এই ভারতী পত্রিকাতেই কবি লিখলেন "কবি কাহিনী" নামক একটি কাব্য। যে বয়সে একজন লেখক - জগতের অন্য সমস্তকিছুকে ভালো করে প্রত্যক্ষ না করে শুধুমাত্র আপন অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই উপলব্ধি করে - এ লেখা ছিল কবির সেই কালের লেখা, তাই এই কাব্যের নায়ক কবি নিজেই। এখানে কবি যে লেখকের সত্তা, তা ঠিক নয় - লেখক নিজেকে যা মনে করতে বা ঘোষনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন - এ লেখা যেন তাই-ই।
"যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন ঊষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য - গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধানের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন ঊষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া। "
অথবা
" প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
ঊষা তার সুখনিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময় - কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা - বালার
সুখময় ঘুম ঘোরে স্বপ্নের মত
কবির বালক - কাল হইল বিগত। "
অথবা
" যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত। "
অথবা
" নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশী,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইত ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর। "
এই কাব্যের প্রতি ছত্রে যেন কবি প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং আপন খেয়ালে প্রকৃতির দু-বাহু উদযাপনে নিজের মনের যে আনন্দ, ঠিক যে ভাবে প্রকৃতির মাঝে তিনি নিজেকে মেলে ধরলে আনন্দ পেতেন - নিজেকে ঠিক সেই ভাবেই প্রকাশ করেছেন। তাই এই কাব্যে তিনি নিজেই যেন নায়ক। "তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে" বা " সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত / কবির বালক কাল হইল বিগত" বা " বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা / প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।" বা "তুমিও তাহার সাথে মিলাইত ধ্বনি, / সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।" এখানে সর্বত্রই কবি এই বাল্য বয়সেই প্রকৃতির আন্তরিকতার সাথে নিজেকে একাত্ম করেছেন এবং বালক মনের অন্তর্জগৎ যেন প্রকৃতির সাথে এক সুরে সুর মিলিয়ে আত্মিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু লেখার আন্তরিকতা এবং আবেগের সাথে জীবনের অভিজ্ঞতার যে মিশেল তা এই কাব্যে অনুপস্থিত। তাই নিজের আবেগের জায়গাটিকেই এই কাব্যে প্রধান রূপে দেখান হয়েছে।
"কবি - কাহিনী" এই কাব্য প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন - " যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সমান নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময়- সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।
কোনো একদিনের বিকেল বেলার ঘটনা। বালক কবি জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর শেষ বিকেলের নিবে আসা আলোয় পায়চারি করছেন। দিবাবসানের প্রহরে যখন সূর্যাস্তের শেষ আভাটি এসে কবির চোখে ধরা দিল - সেই মুহূর্ত যেন কবির মনোজগতে এক বিশেষ ক্ষণ রূপে ধরা দিল। কি যেন চকিতে ঘটে গেল কবির মনে। এক অপরূপ সুন্দরের মাঝে তিনি নিজেকে উপলব্ধি করলেন। আশে পাশের বাড়ির দেওয়াল, পাঁচিল, পুকুরপাড়, মাঠ সবই যেন সৃষ্টিশীলতার এক অনিকেত মুহূর্ত হয়ে বালক কবির মনে ধরা দিল। কবি পড়লেন অন্তঃদ্বন্দ্বে। তিনি ভাবতে লাগলেন - তাঁর চেনা জগতের উপর থেকে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠে গেল - সেকি কেবলমাত্র সন্ধ্যার আলোক সম্পাতের একটি যাদু মাত্র? মনকে বোঝালেন -- তা হতে পারে না! প্রকৃতির এক মুহূর্তকালীন পরিবর্তন শুধু যাদু হতে পারে না -- যদি না সেই মুহূর্তের সাথে কবি মনের কোন যোগাযোগ না থাকে। প্রকৃতির এই তাৎক্ষণিক পরিবর্তন তবে কি তাঁর কবি সত্তার কোনো চঞ্চল মুহূর্ত ! যে মুহূর্ত হঠাৎ-ই তাঁর কবি সত্তা কে মেলে ধরল তাঁর মনের মণিকোঠায়। কবি এই মুহুর্তটিকে ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন -- "আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা - কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের সরূপে দেখিতেছি। সে সরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে - তাহা আনন্দময়, সুন্দর। তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মতো দেখিতে চেষ্টা করিতাম, তখন মনটা খুশি হইয়া উঠিত। "
সে সময় প্রায়শই কবি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন- রাস্তা দিয়ে মুটে মজুর, ছেলে, বুড়ো, মেয়ে মানুষ যারাই যাতায়াত করত - তাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাদের মুখাবয়ব সবই যেন তাঁর কাছে ভারি আশ্চর্য বোধ হতো; মনে হতো যেন সকলেই অনন্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে অবিরত তরঙ্গের মতো বয়ে চলেছে। শিশুকাল থেকে কবি যা কিছু চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন - তা সবই যেন এখন এই বালক বয়সে এসে - সমস্তটুকুকে চৈতন্য দিয়ে দেখত আরম্ভ করলেন। রাস্তা দিয়ে যখন দু-জন যুবক একে ওপরের কাঁধে হাত রেখে স্ফুর্তি করতে করতে চলে যেত - কবি সেই ঘটনাকে সামান্য বলে মনে করতে পারতেন না -- সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন -- "বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকেই যেন দেখিতে পাইতাম।"
এক ভোরবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবি দেখছেন আর ভাবছেন -- সদর স্ট্রীটের রাস্তটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে বোধহয় ফ্রি - স্কুলের বাগানের কিছু গাছ দেখা যায়। সেই গাছ-গাছালির পাতার ফাঁক দিয়ে তখন সূর্যোদ্বয় হচ্ছিল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ - ই এক মুহূর্তকালে কবির চোখের উপর থেকে যেন পর্দ সরে গেল। তিনি লিখছেন - "দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্চুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই" নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দ-রূপের উপর তখনও যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনই হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। "
বিভিন্ন কাজের মুহূর্তে মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে গতি বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় তা কবির মনে এই বালক বয়সে - বিভিন্ন মুহূর্তে -
' মানব দেহের চলনের সংগীত ' রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। এই গতি এই গতিময় ছন্দ যেন তাঁর আপন জগতে এক ছন্দময় বাস্তবতার সৃষ্টি করতে থাকে -- যা ছিল তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনীর অন্যতম উৎস। তিনি এই বিভিন্ন মুহূর্তকে স্বতন্ত্র হিসেবে না দেখে এক সমষ্টিগত হিসেবে দেখতেন। যে মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বত্র নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠত- সেই মুহূর্তে কবি মনের যে উত্থান যে তরঙ্গ তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন -- " সেই ধরণী ব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎ ভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য -- নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিষ্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।
হৃদয় আজই মোর কেমনে গেল খুলি --
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি --
ইহা কবি কল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না। "
********************
(পঞ্চম পর্ব )
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই-
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ,
তোমার হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসার ভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে সরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই।
১৯০১ সাল,
বালক বয়স থেকে যৌবনের প্রাক্কালে কবি রচিত বিভিন্ন কাব্যে ও গানে আমরা বারবার সেই শিশু বয়সেরই অন্বেষণ যেন খুঁজে পাই। ধরার মাঝে অধরাকে প্রত্যক্ষ করার যে বাসনা কবি মনে সুপ্ত হয়ে ছিল তা তাঁর গান ও কাব্যকলমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে অবিরত। শিশু বয়সের ভৃত্য পরিবেশ্টিত যে অনুশাসন এবং যে অনাদর তা কবির মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। শিশু বয়সের যে শৃঙ্খল তা তিনি বরাবর ভাঙতে চেয়েছেন তাঁর বাল্য ও যৌবনের কাব্য সৃষ্টিতে। সংসারে থেকেও যে দূরের দর্শন, তা কবিকে নাড়া দিতে থাকে ভীষণ ভাবে। তাই তো দক্ষিণমুখো জানালা অথবা ছাদের কার্নিস অথবা ঘাট বাঁধানো পুকুরপাড় কবিকে নিয়ে যেত আপন খেয়ালের মনোজগতের পাকদণ্ডীতে - যেখানে থাকত কাব্য সৃষ্টির জন্য হাজারও মণি মাণিক্য। তাই উপরিউক্ত পূজা পর্যায়ের (উপ পর্যায় : অন্তিম বা শেষ) গানটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই - সংসারের মাঝে থেকেও প্রভুর পা'য়ে আপন মন প্রাণ সঁপে দিয়ে কবি অনুভব করেছেন জীবনের মাঝে - দুঃখ শোক, মৃত্যু যন্ত্রণা বা বিচ্ছেদ এসবই যেন আপেক্ষিক ; যেখানে এই শোক অনুতাপের কোনও মানে নেই, জীবনটাই যেন সব, প্রাণটাই সেখানে মুখ্য - তাই সেখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো মৃত্যু নেই। অথচ প্রভুর সংস্পর্ষ বিমুখ হওয়া মাত্রই তিনি ডুবে যান গভীর শোকে, দুঃখে, মৃত্যু যেন অন্তিম হয়ে ঘনিয়ে আসে জীবনের নানা পর্যায়ে। প্রভুর চরণেই আছে একমাত্র পূর্ণতা, সে অনুভব ভয়হীন - তাই-তো চরণস্পর্শ পাওয়ার জন্য কবি মন বারবার কেঁদে ওঠে। জীবনের মাঝে প্রভুকে যদি স্পর্শ করতে পারেন, যদি প্রভুস্পর্শের অনুভব হয় চিরসত্য - তবেই এই ধারার মাঝে চিরমুক্তি যেন অনিবার্য, সংসার ভার, আত্মগ্লানি সব যেন হারিয়ে যায় এক লহমায়। এভাবেই কবি সংসারের মাঝে থেকে, সীমার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে অসীমকে ছুঁয়েছেন, অধরাকে ছুঁয়েছেন, শিশু মানস জগতের শৃঙ্খলাকে ভেঙেছেন এক অনিবার্য রূপে - তার কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে।
তবে তিনি এই সীমার মাঝে অসীমকে ছুঁতে গিয়েও তাঁর কাব্যে তিনি ফিরে এসেছেন আবারও সীমার মধ্যে। আবারও সংসারে, স্নেহের আলিঙ্গনে।
একবার সদলবলে কবি যাত্রা করলেন কারোয়ারের সমুদ্রতীরে। সেখানে তিনি লিখলেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে একটি নাট্যকাব্য। সেই নাট্যকাব্যের নায়ক 'সন্ন্যাসী' সমস্ত স্নেহ, মায়া, মমতাকে তুচ্ছ করে সকল বন্ধন ছিন্ন করে - প্রকৃতিকে জয় করে একান্ত শুদ্ধ রূপে অনন্তকে উপলব্ধি করতে চাইলেন। অনন্ত যেন সকল বন্ধনের বাইরে। অনন্তের অমোঘ আকর্ষণ সন্নাসীকে পথে টেনে আনল। অবশেষে একটি বালিকা তাঁকে স্নেহ, মমতা দিয়ে আবদ্ধ করে অনন্তের ধ্যান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ফিরে আসার পর সন্ন্যাসী দেখলেন - ক্ষুদ্রকে নিয়েই বৃহৎ, সীমাকে নিয়েই অসীম, প্রেমকে নিয়েই মুক্তি- স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেমের আলিঙ্গনই সহজ সত্য, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তির স্বাদ, অনন্তের স্বাদ। তাইতো কবি লিখলেন - "প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।" কবি আরো লিখছেন - "প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্র বেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিত ভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষ বোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে, কি করিয়া! এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা - সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। "
প্রকৃতির প্রতিশোধে - একদিকে সাধারণ গৃহী গ্রামবাসি এবং অন্য দিকে সন্ন্যাসী, - প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদাভেদ ঘুচে গেল, গৃহীর সাথে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটল - তখনই সীমায় এবং অসীমে মিলিত হয়ে সীমার মিথ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যে শূন্যতা যেন দূর হয়ে গেল। পরবর্তীতে রবি লিখেছেন - "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"
চৌরঙ্গীর কাছে সারকুলার রোডের বাগান বাড়িতে কবি যখন বাস করতেন তখন তাঁর বাড়ির দক্ষিণে একটি মস্ত জানালা ছিল। দক্ষিণের দোতলার সেই জানালা দিয়ে কবি বাইরের লোকালয়ের দৃশ্য উপভোগ করতেন। বিভিন্ন মানুষের সারাদিনে বিভিন্ন কাজ, বিশ্রাম, খেলা, আনাগোনা তাঁর ভারি ভালো লাগত, কবির মানস জগৎ ভরে উঠত নানান রসদে - যেন তা ছিল কবির অনুভবে, বিচিত্র গল্পের মতো। নানাপ্রকার দৃশ্যকে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতেন। এক একটি ভিন্ন ছবিকে তিনি কল্পনার আলোকে, মনের আনন্দ দিয়ে ঘিরে ফেলতেন। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে কবির চোখে ধরা পড়ত। এমনি করেই কবি তাঁর মনের ঘরে এক একটি ছোট ছোট দৃশ্যকল্প তৈরি করতেন। সে দৃশ্যকল্প যেন, এক একটি সদ্য প্রস্ফুটিত চিত্র যা এঁকে ফেলার আকাঙ্খা মাত্র। তা ছিল, চোখ দিয়ে মনের জিনিসকে ও মন দিয়ে চোখের দেখাকে দেখতে পাওয়ার ইচ্ছামাত্র। কবি তখন পর্যন্ত তুলির টানে ছবি আঁকতে পারতেন না। না হলে হয়তো পটের উপর রঙ দিয়ে তিনি উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে কবি তখনও স্পষ্ট রেখার টান দিতে অপারগ ছিলেন, তাই যেন সেই কথার রঙ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তা হলেও - ছেলেরা যখন প্রথম রঙের বাক্স উপহার পায় তখন, যেমন তেমন করে ছবি আঁকার চেষ্টা করতে থাকে, কবি ও সেইদিন নবযৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নতুন করে পেয়ে আপনমনে যেন কেবলই রকম - বেরকম ছবি আঁকার চেষ্টা করতেন। কবি লিখেছেন - "তখনকার দিনগুলো নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে, কী আমার গদ্যে পদ্যে, কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তখন যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাজে চলিয়া যাইত, আমি চাহিয়া দেখিতাম - এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দূর-প্রবাসের অতথির মতো অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত। "
কবির শিশু বয়সে ভৃত্যদের শাসন কালটা তাঁর কাছে কখনই সুখকর ছিল না। দুঃখ করে লিখেছিলেন ভারতবর্ষে- দাস রাজাদের রাজত্বকালের ইতিহাস সুখকর না থাকলেও রাজাদের পরিবর্তন ঘটেছে বারবার, কিন্তু কবির ভাগ্যাকাশে সকল কিছুতেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটে নি। তিনি বলেছেন - "পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম, সংসারের ধর্মই এই - বড় যে সে মারে, ছোট যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোট যে সেই মারে, বড় যে সেই মার খায় - শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।" কবি বারবার এক মনে ভেবেছেন - ভেবে কষ্ট পেয়েছেন - যে ভৃত্যদের হাত থেকে কেন এমন নির্মম ব্যবহার তারা বা ছোটরা পেতেন ! কিন্তু ছোটরা তো স্নেহ দয়া মায়ার অযোগ্য ছিল না! সেই বয়সেও এই চিন্তা কবির চিত্তকে ব্যাথিত করত। আসল কারণটা অবশ্য তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। ভৃত্যদের উপরে সম্পূর্ণ ভার ছিল ছোটদের দেখভাল করার। এই সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা পরমাত্মীয়ের পক্ষেও দুর্বহ। "ছোট ছেলেকে যদি ছোট ছেলে হইতে দেওয়া যায় - সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতুহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলে সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে ছেলেমানুষ ছেলেমানুষির দ্বারা নিজের যে ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসন কর্তার উপরে পড়ে। তখন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ানো হয়। যে বেচারা কাঁধে করে, তাহার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে, কিন্তু ঘোড়া - বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে। "
বাড়ির বাইরে শিশুদের যাওয়ার বারণ ছিল, এমনকি ভিতরেও যে সর্বত্র অবাধে বাড়ির ছোটরা যাতায়াত করতে পারত - এমনটা নয়। কবি তাই আড়াল থেকেই তাঁর চারপাশের জগতকে তাঁর মানস জগতের অদ্ভুত সংমিশ্রণে উপলব্ধি করতেন। বাইরের যে একটা অনন্ত প্রসারিত প্রসাদ তা পাওয়া ছিল কবির কাছে অতীত, অথচ সেই অদেখা প্রসাদ - তার রূপ, রস, গন্ধ, বন্ধ জানালার ফাঁক ফোকর কবির মনোজগতকে ছুঁয়ে যেত অবিরত। সেই চিরায়ত প্রসাদ যেন গরাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে নানান ইশারায় কবির মনের কাছাকাছি আসতে চাইত। সেই প্রসাদ ছিল মুক্ত, কবি ছিলেন আবদ্ধ - মিলনের উপায় না থাকায় সেই প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। কবি লিখছেন - " আজ সেই খড়ির গণ্ডী মুছে গেছে, কিন্তু গণ্ডী তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।" এই যন্ত্রণা কবি যৌবনকাল অবধি নিয়ত বহন করে বেড়াতেন, তার মনের যে পরিযায়ী বাসনা তা তাঁর শিশুকালে অবদমিত অবস্থায় একপ্রকার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। কে বলতে পারে যদি তিনি শিশুকালে সুবিচার পেতেন তবে তাঁর মনোজগৎ আরো কোনো সুচারু কাব্যের হদিশ দিত না! আরো কোনো শিশু কাব্য আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত না! শিশু বয়সের এই অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে বড় হয়ে কবি লিখলেন
খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে ।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি, আয়,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরেবিলে ।'
বনের পাখি বলে, ' না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, ' হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।' "
বাড়িতে কবির সমবয়স্কা খেলার একটি সঙ্গিনী বালিকা ছিল। সেই বালিকা, কবিকে" রাজার বাড়ি" বলে বাড়ির মধ্যেই একটি জায়গার হদিস দিত। কিন্তু শিশু কবি মন বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরেও সেই রাজার বাড়ির হদিস করতে পারত না। বালিকা যখন বলত - আজ রাজার বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন কবি ব্যথিত হতেন ভাবতেন যে তার কপালে এমন শুভ যোগ নেই যে তিনি বালিকার সঙ্গী হতে পারেন। " সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য, খেলার সামগ্রী তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে ; একতলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায় ; কিন্তু কোনো মতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?' সে বলিয়াছে - 'না, এই বাড়ির মধ্যেই।' আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়! রাজা যে কে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকু মাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি। "
এরপর কবিকে পাই তাঁর স্কুলের গণ্ডীতে - 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি।' কিন্তু স্কুলের ধরা বাঁধা একঘেঁয়ে জীবন বোধহয় কবির জন্য ছিল না। তাই স্কুলের পড়াশোনা দিনের পর দিন তাঁর কাছে অসাড় হয়ে উঠতে থাকে। ওরিয়েন্টালে পড়াকালীন - কেবলমাত্র ছাত্র হয়ে থাকার যে হীনতা তা মেটাবার জন্য কবি একটি উপায় বের করেন। বাড়ির বারান্দায় একটি বিশেষ কোণে ছিল কবির ক্লাসঘর। রেলিংগুলো ছিল কবির ছাত্র আর একটি লাঠি হাতে নিয়ে চৌকি নিয়ে তাদের সামনে বসে মাস্টারি করতেন। রেলিংগুলোর মধ্যে কে ভালো, কে মন্দ, স্থির করাই ছিল । ভালোমানুষ রেলিং, দুষ্টু রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিং এর প্রভেদ কবির কাছে সুস্পষ্ট ছিল। দুষ্টু রেলিংগুলোর উপর ক্রমাগত লাঠির বর্ষণ তাদের এমনিই দুর্দশা ঘটিয়েছিল, যে প্রাণ থাকলে তারা বোধহয় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শান্তি পেত। এসবই ছিল শিশু কবি মনের দৌরাত্ম্য। অনিমেষ আনন্দে পুরো স্কুলকে তিনি তুলে এনেছিলেন বারান্দায়। এ খেলা চিরায়ত, অনেক শিশুর মধ্যেই এখনও আমরা এই শিক্ষক শিক্ষক খেলার প্রবণতা দেখতে পাই। যার মধ্যে দিয়ে শিশু কবি প্রমাণ করতে চান, যে তিনি বড়দের সমকক্ষ। তাঁর বোধ শিক্ষকের সমতুল্য। এই তুল্যমূল্য বিচারের মধ্যে দিয়ে কিন্তু কবির চেতনা সেই অনুশাসনের বেড়াজাল ভেঙে বেরোতে চায়, বাইরের পৃথিবীকে মুক্ত মনে গ্রহণ করতে চায় - প্রকৃতির মোহময় রূপ, যা কিছু তার কাছে অজানা তা এক শিক্ষকের বোধের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান।
ওরিয়েন্টালে বেশিদিন কবি ছিলেন না। এরপর ভর্তি হন নর্মাল স্কুলে। তবে সেখানেও শিশু রবির অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। বিদ্যালয়ের কাজের শুরুতে প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছাত্ররা বসে গানের সুরে কি যেন এক দুর্বোধ্য কবিতা আবৃত্তি করত। শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদের মনোরঞ্জনের কথা মাথায় রেখে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু গানের ইংরাজি কথার সাথে সুরও ছিল তথৈবচ। ছাত্ররা যে কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে বা অনুষ্ঠান করছে তা কবির বোধগম্য ছিল না। অথচ কবির চোখে - ইস্কুলের কর্তৃপক্ষেরা তখনকার কোনো একটা থিয়োরি অবলম্বন করে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁরা ছাত্রদের আনন্দ বিধান করছেন। অথচ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে তার ফলাফল বিচারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যেন তাঁদের থিয়োরি অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়াটাই অপরাধ। সেই গানের কেবল একটি লাইন কবির মনে ছিল - তা হল - "কালোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং ।" অনেক পরে কবি উদ্ধার করেছিলেন এর আসল অর্থ - তবে 'কালোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তা কবির বোধের বাইরে ছিল -
Full of glee, signing merrily, merrily, merrily. "
নর্মাল স্কুলের স্মৃতিও শিশু রবির কাছে মধুর ছিল না। যদি সঠিক ভাবে কবি বন্ধুদের সাথে মিশতে পারতেন তবে হয়তো এই বোধ কবির হোত না। কিন্তু কবি লিখছেন -" অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর - আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে।
শিশু রবির বয়স তখন সাত আট বছর, তার এক ভাগিনেও শ্রী যুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ (বয়স রবির থেকে সামান্য বড়) ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করে খুব উৎসাহের সাথে তখন হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়াতেন। এই জ্যোতিপ্রকাশই প্রথম কবিকে কবিতা লেখার জন্য উৎসাহিত করতে থাকেন। একদিন দুপুরে শিশু রবিকে ঘরে ডেকে বললেন - 'তোমাকে পদ্য লিখতে হবে।' এই বলে পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি কবিকে বুঝিয়ে দিলেন। কবি পরে লিখলেন - " পদ্য - জিনিসটিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবনা চিন্তা নাই, কোনো খানে মর্ত্যজনোচিত দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, একথা কল্পনা করিতে সাহস হইত না।" এরপর " ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেনসিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।" " বিশেষতঃ ; আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুললেন।। " এইভাবে কবির মানস জগতে প্রথম কাব্য লেখায় হাতে খড়ি হল। অচিরেই যে বাসনা শিশু রবি থেকে বৃদ্ধ রবিকে সারাটা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল। সে বন্ধন মুক্ত হওয়ার ছিল না।
কবিতা প্রেম সম্পর্কে যৌবনকালে শিলাইদহ থেকে কবি লিখলেন (৮ই মে, ১৯৯৩- ছিন্নপত্র) - " কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধহয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাকদত্তা হয়েছিল - তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধার, বটের তলা, বাড়ি - ভিতরের বাগান, বাড়ির ভিতরের অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়া গুলো আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করেছিল। তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত - কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা বদল হয়ে গিয়েছিল। " কিন্তু কবিতা নামক সেই মেয়েটি মোটেই কবির চোখে পয়মন্ত ছিল না - কারণ আর যাই হোক, কবিতা কোনদিন সৌভাগ্য নিয়ে আসে না। এখানে কবি কবিতাকে যেন তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য বোধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন - যার বিরহে কবি বিরহী, যার উল্লাসে কবি সোচ্চার, যার অবদমনে কবি অপ্রস্তুত, যার নির্লজ্জতায় কবি উপঢৌকনহীন খোলা পাতা, যার প্রেমে কবি আজন্ম ভিখারি, যার ছন্নছাড়া আবেদনে কবি পথের বাউল। সেই কবিতা সেই কাব্য সেই - ই কবির জীবনের একমাত্র সত্য। কবি বললেন - কবিতা যাকে বরণ করে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কিন্তু এক এক সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃদপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে দেয়। কবিতা নামক প্রেয়সী - যে লোককে নির্বাচন করে, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে - গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসে থাকা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে কিন্তু কবির আসল জীবনটিই তাঁর কাছে কবি বন্দক রেখেছিলেন। কবি লিখেছেন - "জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞতসারে অনেক মিথ্যেবরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে - সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয় স্থান।"
কবির বাল্য বয়সে তখনকার দিনে মজলিস বলে একটি সামাজিকতা খুব চালু ছিল। আগেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিক অবস্থান ছিল মানুষের মধ্যে বাল্যকালে তারই শেষ অস্তচ্ছটা কবি অনুভব করেছিলেন। পরস্পরে মেলামেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং মজলিস ছিল সে সময়ের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। মজলিসী মানুষদের সেকালে খুব কদর ছিল। বর্তমানে লোকেরা, নিজ প্রয়োজনে কাজের জন্য দেখা সাক্ষাত করতে আসে, কিন্তু মজলিসে সময় কাটাতে আসে না। লোকের সময়ও নেই আর সে ঘনিষ্ঠতাও নেই। বাল্যকালে কবির বাড়িতে বহু মানুষের আনাগোনা কবি প্রত্যক্ষ করতেন। হাসি, গল্প, আড্ডায় বারান্দা ও বৈঠকখানা মুখরিত হয়ে থাকত। চারিদিকের নানা মানুষকে নিয়ে খোশ-গল্প জমিয়ে তোলা, হাসি গল্পে উতলা হওয়া - এ একটা শক্তি ছিল বটে - সেই শক্তিটাই যেন আজ কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেছে। মানুষ আছে তবু - সেসব বারান্দা, বৈঠকখানা আজ যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত আসবাব-আয়োজন ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই দশজনের জন্য ছিল ; এইজন্য মানুষে মানুষে যে জাঁকজমক ছিল তা উদ্ধত নয়। কবি তাই পরবর্তীতে আফসোস করেছেন - যে বড়মানুষদের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তা নির্মম, তা নির্বিচারে উদার আহ্বান করতে অক্ষম, খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ - সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করতে পারে না। আমরা আজকাল যাদের নকল করে ঘর তৈরি করি ও ঘর সাজাই, নিজের প্রণালীমত তাদেরও সমাজ আছে এবং তাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। কিন্তু মুশকিল হল - আমরা দেহহিতের জন্য দশজনকে নিয়ে সভা করে থাকি - কিন্তু শুধুমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে নিয়ে জমিয়ে বসা বা মানুষকে ভালো লাগে বলেই সকলকে একসাথে নিয়ে বসা - এখনকার দিনে একেবারেই উঠে গেছে। কবির প্রাপ্তবয়স্ক মন, সে দিনের সেই বাল্য বয়সের স্মৃতি ঘাঁটতে গিয়ে বলেছেন - " এতবড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁরা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজকের দিনে তাহাদিগকে আর - কোনো দেশের (অন্য দেশের) লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"
কবির বাল্যকালের কাব্য চর্চা প্রসঙ্গ উঠলে - জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু, ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কথা সহজেই উঠে আসে। বাল্যকালে কবির কাব্যলোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ ছিলেন এই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধু বাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের অনুরাগের সীমা ছিল ন। উদাত্ত কন্ঠে গানের সাথে, টেবিল চেয়ার, বই ইত্যাদির উপর আঙুলে বোল তুলে গানের আসর জমাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আনন্দ উপভোগ করার শক্তি তাঁর মধ্যে অসামান্য ও উদার ছিল। প্রাণ ভরে রসগ্রহণ এবং মন খুলে গুণগান করার ক্ষেত্রে তিনি কখনই কার্পণ্য বোধ করতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখতেও তাঁর ক্ষিপ্রতা ছিল অসামান্য। এ হেন মানুষ সম্পর্কে রবির কৌতুহলের সীমা ছিল না এবং তার সঙ্গ লাভে বরাবরই রবি পুলকিত এবং আনন্দিত হতেন। 'উদাসিনী' নামে তাঁর একটি কাব্য বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল।
সাহিত্য ভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্য পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। তাই অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ কবির সাহিত্য বোধশক্তিকে সচেতন করে তুলত। অক্ষয়বাবু বালকদের দলে বালকের মতো মিশতে পারতেন। দাদাদের সভা থেকে রবি তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে যেতেন তাদের ইস্কুলের ঘরটিতে। সেখানেও মিট্ মিটে রেড়ির তেলের আলো আঁধারীতে সভা জমিয়ে তুলতে অক্ষয়বাবুর কোনো কুন্ঠাবোধ ছিল না। এই কারণে কবি তাঁর কাছে খুব সহজ ভাবে তাঁর লেখা সমস্ত কাব্য মেলে ধরতে পারতেন, আলোচনা করতে পারতেন। এ যেন বড় ও ছোটদের এক যোগসূত্র। যে যোগসূত্রের মাধ্যমে ক্রমেই কবি নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা চালাতেন। কবি তাঁর কাছে বহু ইংরাজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনেছেন, তাঁকে নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলোচনা করেছেন। কবি লিখেছেন-- " নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়েছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসা লাভ করিয়াছি।"
**********
(শেষ পর্ব )
সজনি গো
শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে ।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুন্ঠত, থরহর কম্পত দেহ
ঘন ঘন রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ ।
আশ্বিন ১২৮৪
বালক বয়সে রবি লিখলেন - মৈথিলী মিশ্রিত কাব্য "ভানুসিংহের পদাবলী", যা কাব্যের ইতিহাসে অন্যতম নজির সৃষ্টি করল। ইং ১৮৮৪ সালে এই কবিতাগুলোই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি প্রকাশের আগে বিভিন্ন সময়ে 'ভারতী' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে জীবনস্মৃতি গ্রন্থের 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে এই কবিতাগুলি বিবৃত করেছিলেন রবি ঠাকুর। মূলত যে ভাষায় রবি, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেন তা হল ব্রজবুলি। পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি। পদগুলিতে মূলত রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় এর নাম ব্রজবুলি বলে ধরা হয় অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের ব্রজভূমি (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) অঞ্চলেও এ ভাষার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।
সে কালে রবি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দ্বারা সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতেন।সংকলনে মৈথিলী মিশ্রিত ভাষা কবির পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল। সেই কারণেই তিনি এই কাব্যরসের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্পর্কে কবি ভাবতেন - একদিন এই কাব্যরসের আবরণ মোচন করতে করতেই একটি - আধটি কাব্যরত্ন ঠিক খুঁজে আনবেন। কবি লিখেছেন - " এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"
অক্ষয়বাবুর কাছ থেকে ইংরেজ বালক কবি 'চ্যাটার্টনের বিবরণ রবি শুনেছিলেন। ষোলো বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন এই কিশোর কবি, টমাস চ্যাটার্টন। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করে কবিতা লিখেছিলেন যে অনেকেই তা ধরতে পারেন নি। কোলরিজ তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন "আ মান ডে অন চ্যাটার্টন, কিটস নিজের " এনডেমিয়ন ' এবং শেলি "অ্যাডোনিস" তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিখ্যাত টেট গ্যালারিতে রাখা হয়েছিল তাঁর বড় প্রতিকৃতি। কিন্তু এইসব হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক পর। ব্রিটেনের গোঁড়া মানসিকতার পাঠকসমাজ তাঁকে সম্মান নিয়ে বাঁচতে দেয়নি। দরিদ্র পরিবার, কল্পনাপ্রবণ এক বালক আর তাঁর মধ্যযুগীয় কবিতার প্রতি অজানা টান ছিল তাঁর জীবনের গল্পের সূত্র। মধ্যযুগীয় কবিতা, কাব্যের ভাষা ও বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। গির্জার এক গোপন প্রকোষ্ঠে পুরোনো আমলের কবিতা পড়ে হুবহু নকল করতে শুরু করেছিলেন তার ভাষা, ভঙ্গি, ছন্দ এবং নকল করেছিলেন পঞ্চদশ শতকের কবিদের হস্তাক্ষর। তারপরেই তাঁর মানসলোকে জন্ম নিলেন রাউলিং নামের এক মধ্যযুগীয় কবি। এই নামের আড়ালে চ্যাটার্টন লিখে ফেললেন অসংখ্য মধ্যযুগের আবহে লেখা কবিতা। প্রকাশ করলেন 'থম্পসন রাউলি' নামে এক মধ্যযুগীয় কবির কবিতা। এই অসাধারণ কবিতা পাঠকের মন ছুঁয়ে গেল। কিন্তু টমাস চ্যাটার্টন পাঠকের কাছে নিজের আসল পরিচয় দিতে পারলেন না। কারণ নিছক রহস্যের জন্য বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন জাল দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে। বহু পণ্ডিত সেই ছলনা ধরতে ব্যর্থ হন। কিন্তু যখন বিষয়টির রহস্য উন্মোচিত হল, তখন ব্রিটেনের পাঠক সম্প্রদায় চরম অপমান করেছিলেন এই উদীয়মান কবিকে। প্রকাশক-রাও সরে গিয়েছিলেন পাশ থেকে। তিনবছর জীবিকা নির্বাহের ব্যর্থ চেষ্টা করে, মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন এই কবি।
এই কবির গল্প শুনে প্রায় একইরকম কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন বালক রবি। "গহন কুসুম কুঞ্জ - মাঝে" লেখার পর রবি তাঁর বন্ধুকে বললেন "সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলে বন্ধুকে তাঁর কবিতা শোনালেন। শুনে তিনি ভীষণ রকম বিচলিত হয়ে বললেন -" এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি - চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয় বাবুকে দিব। " তখন রবি খাতা দেখিয়ে স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলেন - এ লেখা বিদ্যাপতি - চণ্ডীদাসের হাত দিয়ে নিশ্চয়ই বের হয়নি, এ লেখা তাঁর নিজের। বন্ধু গম্ভীর হয়ে তখন বললেন -" নিতান্ত মন্দ হয় নাই। "
তখন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানী থেকে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে তুলনা করে আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্পর্কে একখানি চটি বই বের করেন। তাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তা রূপে যে সম্মান দেন তা কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে সহজে জোটে না। এই চটি বইখানি লিখেই নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় "ডক্টর" উপাধি লাভ করেন।
রবি পরে লিখেছেন - ভানুসিংহ যেই-ই হোক না কেন, তাঁর লেখা যদি বর্তমান তাঁর হাতে পড়ত তবে তিনি নিশ্চয়ই ঠকতেন না ; এ কথা জোর দিয়েই তিনি স্বীকার করেছেন। এই কাব্যের ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ এ ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা নয়, একটি কৃত্রিম ভাষা ; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে এ ভাষার কিছু না কিছু পরিমার্জন বা পরিবর্ধন ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের ভাবের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। কবি লিখেছেন - "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাংমাত্র।"
গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি,আও আও লো।
তখনও হারমোনিয়াম আসেনি এ দেশে। শিশু রবির পড়াশোনার যিনি তদারকিতে ছিলেন তিনি বুঝেছিলেন ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর হাল্কা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে শিশু মনে সহজেই জায়গা করে নেয়। তাছাড়া গানের বা কবিতার দিশি তাল বাঁয়া তবলার বোলের তোয়াক্কা না করে - নাড়ীতে নিজের মতো আনন্দে নেচে ওঠে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো শুরু হয় মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভোলানো গান শেখানোর শুরুও সেই ছড়ায়। এইভাবেই কবি মনের আনন্দে ছড়ার ছন্দে, আপন গানের বোলে বেড়ে উঠছিলেন। তখন কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করার চল ছিল। শিশু রবি ইচ্ছেমত কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেতেন তাই দিয়েই তার গান শেখার ঝুলি ভর্তি করতেন। মন দিয়ে গান শেখা কবির ধাতে ছিল না। তখন গানের শিক্ষাকর্তা ছিলেন কবির মেজদাদা। তবু বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শেখা কবির শিশুকাল থেকে। ব্রহ্মসংগীত ও তখন তিনি একটু আধটু শিখতে শুরু করেছেন। সেজদাদা যখন গাইতেন রবি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে মনের মধ্যে সে গানের ছাপ তুলে নিতেন আর সন্ধ্যাবেলা মাকে সেই গান শুনিয়ে রবি অবাক করে দিতেন। তখন বাড়িতে শ্রীকন্ঠ বাবু দিনরাত গানের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলীর তেল মেখে স্নান করতেন ; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে ; গুন্ গুন্ গান চলত, বাড়ির ছেলেদের গানের টানে বেঁধে রাখতেন তার চারপাশে। তিনি কখনই গান শেখাতেন না, নিজে গাইতেন, গান দিতেন - আর গুন্ গুন্ করতে করতে রবি কখন যেন সেই গান তুলে ফেলতেন। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠে, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড় বড় চোখ জ্বল্ জ্বল্ করত, গান ধরতেন -
" ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী "
আর সাথে রবিকেও গেয়ে উঠতে হত। এই ছিল রবির গান শেখার প্রথম পাঠ।
সেকালে আতিথ্য ছিল খোলা দরজার। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথা নিয়মে। অচেনা অতিথি একদিন লেপ মোড়া তম্বুরা কাঁখে ক'রে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোদরবারে যথারীতি তাঁর হাতে হুঁকো তুলে দিত। সেকালে অতিথিদের জন্য যেমন তামাক তেমনই পানের ব্যবস্থা থাকত রবির বাড়িতে। বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কাজ ছিল অতিথিদের জন্য রোজ রাশি রাশি পান সাজা। চট্ পট্ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমত মসলা ভ'রে, লবঙ্গ মুড়ে, সেগুলো বোঝাই হয়ে যেত পিতলের গামলায় ; উপরে পড়ত খয়েরের ছোপ লাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটিতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাইঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগালোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ীর মধ্যে গোলাপ জলের গন্ধ। আর বাড়িতে যারা আসতেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম "আসুন মহাশয়" ডাক পেতেন তার সাথে অম্বুরি তামাকের গন্ধ বিনি পয়সায়। এভাবেই চলছিল রবির বেড়ে ওঠা। অতিথিবাৎসল্য ছোটবেলা থেকেই রবির মনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল। আর সহজ সরল গানের আলাপ শুনতে শুনতে কখন যে রবি গানের পরিবেশকে আপন হৃদয়ে স্থান দিয়ে ফেলেছিলেন তা বোধহয় কবির নিজেরও অজানা ছিল। এবার শুরু হল, সেই গানের আলাপের মধ্যে, সুরের মাদকতায় মন হারানোর পালা। সেই সুরের মধ্যে শুরু হল একটু একটু করে গানের কথা বসানোর খেলা। আর সে খেলায় যে না মজেছে, সে তো জানেই না - বাঁচার আসল মানে!
রবির শিশু থেকে বালক হয়ে ওঠার রোজনামচায় চোখ রাখলে দেখতে পাওয়া যায় এক কঠিন নিয়মানুবর্তিতা। দিনের প্রতিটি ধাপে ব্যস্ততা। প্রতিটি প্রহরে কবি সত্তার সাথে অনুশাসনের এক বিতর্কিত ও বিরল সহাবস্থান। সেখানে চিন্তার অবকাশ ছিল কম, অভ্যাসের দাসত্ব ছিল মাত্রাতিরিক্ত। হয়তো এই অনুশাসনই কবির পরবর্তী জীবনকে এক সু-শৃঙ্খল যাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ভোরবেলা উঠেই খানিক পালোয়ানের সাথে আখড়াতে কুস্তির প্যাঁচ পয়জার। কিন্তু রবির মায়ের কাছে মাটি মাখা ফর্সা ছেলের ধূসর অবয়ব মোটেই কাঙ্খিত ছিল না। তাই ছুটির দিনে চলত - রবির ঝাড়াই মোছাই। বাদাম বাটা, দুধের সর, কমলালেবুর খোসা ইত্যাদি আরো কত কি, শিলে পিষে মলম বানিয়ে ছুটির দিন কবির সারা অঙ্গে প্রয়োগ হত, পাছে রঙ কালো হয়ে যায়। রবিবারের সেই ত্বক চর্চার ঘটা দেখে কবি লিখেছেন - এইসব বাটার তত্বকথা যদি তিনি জানতেন - তবে বেগমবিলাস নাম দিয়ে ব্যবসা করলে বোধহয় সন্দেশের দোকানের চেয়ে বেশি লাভ করতেন। আর রবির মন উতলা হয়ে উঠত ছাড়া পাওয়ার জন্য। সেকালে ইস্কুলের ছেলেদের কাছে একটা গুজব ছিল যে - জন্মমাত্র নাকি ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, আর তাতেই রঙটাতে যেন সাহেবী জেল্লা লাগে। কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাতে আসতেন মেডিকেল কলেজের এক ছাত্র। দেউড়িতে সাতটা বাজলে ছিল - নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি ধরা এক নিরেট সময়ে উপস্থিতি। কালো বোর্ডের উপর ছড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায় - পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত ইত্যাদি। এরপর সীতার বনবাস থেকে মেঘনাদবধ কাব্য। সাথে আবার প্রাকৃত বিজ্ঞান। এরপরে কিছুদিনের জন্য হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন। কিছু না বুঝে "মুগ্ধবোধ" মুখস্থের পালা। এভাবে যতই পড়ার চাপ বাড়ে - শিশু মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু মনের বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে যেন মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায় ; তবু নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো ছিল না। অঙ্ক কষতে কষতে রবির মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর শ্লেট আড়াল করে নীচের দিকে তাকিয়ে রবি দেখে - দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলেছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন পরা ছিপ্ ছিপে ছোকরা দারোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সক্কালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্য বোধও জেগে ওঠে - ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া। এতো কিছু নিয়ম কানুনের বেড়া জাল কেটে তবু ছুটি চায় রবির মন ।হারিয়ে যেতে চায় ফাঁকা মাঠে যেখানে আকাশের নীল ভার মুক্ত করে দেয় সমস্ত বন্ধনকে। শিশু রবি, ফেলে দেওয়া আতার বীজ পুঁতে রাখে বারান্দার এক কোণে, রোজ নিয়ম করে জল দিয়ে অপেক্ষা করে থাকে চারাগাছের জন্য। যেন চারাগাছের কচি পাতায় রবির মুক্তি লেখা থাকে অনায়াস। সূর্য যখন আঙিনায় হেলে পড়ে, ন'টা বাজে - বেঁটে গোবিন্দ হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আসে, রবিকে নিয়ে যায় চান করাতে। সাড়ে ন' টায় জুটে যায় রোজের বরাদ্দ ডাল, ভাত, মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। খাওয়ার অরুচি কোথাও লেখা হয় না শুধু শিশু মনে দাগ রেখে যায় পুড়ে যাওয়া বাসনের রঙের মতো। ঘন্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন উদাস করা ডাক শোনা যায় কাঁচা আম ওয়ালার। বাসন ওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলে যায় দূর থেকে আরো দূরে। যেন রবির মনকে নিয়ে যায় কোন অচিন দেশে - যেখানে বাসন ওয়ালার ডাক বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে এক ছুটির কথা বলে যায়। গলির ধারের বাড়ির ছাদে বড়োবউ ভিজে চুলে মাখতে থাকে সকালের রোদ্দুর, তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলে চলে অনবরত। যেন এক তাড়া বিহীন জীবন। সেকালে মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার তাগিদ সে ভাবে ছিল না, তাই ছোট্ট রবি ভাবত - মেয়ে জন্ম নিছক সুখের। অবশেষে বুড়ো ঘোড়া পাল্কি গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল দশটা - চারটের আন্দামানে, ইস্কুলে। সাড়ে চারটেয় ইস্কুল থেকে ফিরেই বিকালে, জিমনাসটিকের ক্লাস। কাঠের ডাণ্ডার উপর শরীর নিয়ে ওলোট পালট পর্ব। জিমনাসটিকের মাস্টার যেতে না যেতেই এসে পড়ত - ছবি আঁকার মাস্টার। ক্রমে নিবে আসে দিনের আলো, অন্ধকারে ডুবতে থাকে ইঁট কাঠের বড় বাড়িটা। পড়ার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টারের উপস্থিতি জানান দেয় - কালো কালো মলাটের ইংরেজি রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। শুরু হয় ইংরেজি শিক্ষার ক্লাস। রবি ঢুলতে থাকে, ঢুলতে ঢুলতে চমকে ওঠেন। যত না পড়েন তার চেয়ে না-পড়েন অনেক বেশি।
রবির জীবনে প্রধান ছুটির দেশ ছিল তার বাড়ির খোলা ছাদ। শিশুকাল থেকে বড় বয়স পর্যন্ত রবির নানা রঙের দিন ঐ ছাদের টানে বয়ে গেছে। রবির বাবার ঘর ছিল তেতলার ঘরে। সূর্য যখন তার লালের আভা ছড়িয়ে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রেখে ধীরে ধীরে পূব আকাশে ফুটে উঠত সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে রবি বহুদিন চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতেন - তাঁর পিতৃদেব সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে উপাসনায় বসেছেন, কোলে দুটি হাত জোড়া করা। মাঝে মাঝেই তিনি চলে যেতেন পাহাড়ে আর তারই সাথে বয়ে যেত কবির মন। সবুজের দেশে, পাহাড়ি ফুলের দেশে, শ্বেতশুভ্র হিমালয়ের কোলে কবির মন হারিয়ে যেত অজানার পথে। ছাদের উপর থেকে কবি লক্ষ্য করতেন লোকজনের যাতায়াত , সামনের বসতির দিন যাপন, ঘন লোকবসতির মাথার উপর দিয়ে কবির মন যেন ডিঙিয়ে চলত দূরে বহুদূরে, যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। বরাবরই এই দুপুর বেলাটা কবির মনকে চুরি করে নিয়ে যেত, তিনি হারিয়ে যেতেন তার স্বপ্নরাজ্যে - এ যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে বাবার ঘরের ছিটকিনি খুলে ফেলতেন - সামনে বড় সোফা - একলা হয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। বাবার স্নানঘরে ভারি অদ্ভুত একটি ব্যাপার ছিল - সেখানে উপর থেকে কলের ঝরনা দিয়ে জল গড়াত। কবি সেই ঝরনাতলায় দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ভিজতেন - এ যেন ছুঁতে চাওয়া, বাবার কাছাকাছি পৌঁছাতে চাওয়া। কাব্যিক সত্তাগুলো তখন ঝর্নার জলে ধুয়ে গিয়ে মিশে যেত খাল বিল পুকুর নদীতে। প্রকৃতিতে কবি সত্তা একাগ্র চিত্তে বয়ে যেত এক অনিমেষ উপন্যাস লিখবে বলে। ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। গলির শেষ মাথা দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। ফেরিওয়ালারা হাঁটতে হাঁটতে খানিক জিরিয়ে নিত বাড়ির তলায় বসে। সারা দুপুর জেগে থাকত ঘুঘু পাখির ডাক। চোখ বুজে শুনলে সে ডাক মিশে যেত গ্রীষ্মের দুপুরের আম ডালের পাতায় পাতায়। হঠাৎ চুড়িওয়ালার ডাক এসে পৌঁছাত অন্দরমহলে, যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ। দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমত বেলোয়ারি চুড়ি । কবি লিখছেন - " ছাদটা ছিল আমার কেতাবে পড়া মরুভূমি, ধূ ধূ করছে চারদিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।" এক একদিন বাড়ির উঠোনে আসত ভাল্লুক নাচ-ওয়ালা, মাদারী ঘোড়া ওয়ালা - উঠোনে চাবুক পড়ত চটাস্ চটাস্ , সাপুড়ে আসত সাপ খেলা নিয়ে। সে সব দিন ছিল বড় আনন্দের। রবির সারা জীবনের সঙ্গী ছিল সে সব দিন। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের কড়িও যেমন রঙ মিলিয়ে এক হয়ে থাকে, তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে কবির মন ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে যেত দিনান্তের সূর্যাস্তে।
বাড়িতে নতুন আইন চালালেন বাড়ির কর্ত্রী। কবির বউঠাকুরনের জায়গা হল বাড়ির - ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত ছেলেমমানুষ রবি। ভালো রাঁধতেন বউঠাকুরন, ভালোবাসতেন খাওয়াতে, সব খাওয়ানোর শখ মেটাতেন রবির উপর। ইস্কুল থেকে ফিরে রবির জন্য তৈরি থাকত - চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি আর পান্তা ভাত, সাথে অল্প একটু লঙ্কার আভাস আর আমের আচার। বউঠাকুরন যখন কোনো আত্মীয় বাড়ি যেতেন, ইস্কুল থেকে ফিরে ঘরের সামনে তার কোনো চটিজোড়া দেখতে না পেয়ে কবি ভারি রাগ করতেন। রাগ করে ঘরের থেকে কোনো একটা দামী জিনিস লুকিয়ে রাখতেন। আর এইভাবে সূচনা করতেন এক অভিমানী ঝগড়ার। কবি বলতেন - "তুমি গেলে ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার!" বউঠানও রাগ দেখিয়ে বলতেন, " তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।"
এবার ছাদের রাজ্যে যেন নতুন ঋতু উপস্থিত হল। তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোর বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। কবি জায়গা পেলেন তারই এক কোণের ঘরে। সেকালে বড় ছোটর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু সেই পুরনো কায়দার ভিড়ের মধ্যেও জ্যোতিদাদা এলেন একেবারে নির্জলা নতুন মন নিয়ে। কবি ছিলেন তাঁর থেকে বারো বছরের ছোট। বয়সের এতো দূরে থেকেও কবি - জ্যোতিদাদার চোখে পড়তেন। তাঁর সাথে আলাপ করতে গিয়ে - জ্যাঠামি বলে - কোনোদিন জ্যোতিদাদা কবির মুখ চাপা দেননি। তাই কবিও ছিলেন তাঁর কাছে অকুতোভয়।
এরপর ছাদের ঘরে পিয়ানো এল। আর এল হালফ্যাশানের বার্নিস করা বউবাজারের আসবাব। কবির মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এইবার ছুটল গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর দুই আঙুলের ঝড় তুলে তৈরি করতে থাকলেন নতুন নতুন সুর, আর ছুটে চলা সুরে নিত্যনতুন কথা বসিয়ে গান বেঁধে রাখবার দায়িত্ব বর্তালো কবির উপর। দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। পারিবারিক আড্ডার আসর। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালায় ভিজে রুমাল, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল, আর বাটাতে থাকত ছাঁচি পান।
বউঠাকুরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন, পাৎলা চাদর, মচমচে চটিতে সজ্জিত হয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা ; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আর কবি চড়া সুরে ধরতেন গান। বিধাতার দেওয়া সুরটুকু রবি উজাড় করে দিতেন সন্ধ্যের আকাশে। ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত সেই গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় আকাশ যেত ভরে । ছাদটাকে বউঠাকুরন নিজের মতো নিজের হাতে গাছে গাছে সাজিয়ে তুলেছিলেন। পিল্পের উপর সারি সারি লম্বা লম্বা পাম গাছ; আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা । ছাদ জখম হতে পারে একথা কেউ মনেই স্থান দেননি - সেই দিন ছিল যেন এক খাম খেয়ালির স্বপ্নরাজ্য।
জমিদারির কাজ দেখতে একবার জ্যোতিদাদাকে যেতে হল শিলাইদহে। দরকারে পথে বেরোলেও, রবিকে সঙ্গে নিতে জ্যোতিদাদা কিন্তু ভোলেননি। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' জ্যোতিদাদা কিন্তু তার ভালোবাসার রবির জন্য ভেবেছিলেন- ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ যেন একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন - রবির ছিল বাতাসে উড়ে বেড়ানোর মতো মন, গাছপালা মাটি জল সেসব ছিল রবির মনের খোরাক, আর তা থেকেই জন্ম হতে পারে কিছু অনবদ্য শব্দ মুহূর্ত । হাজার কাজের মধ্যেও জ্যোতিদাদা, রবির খেয়াল রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করতেন - একলা মন নিয়েই রবি যেন ভালো আছেন। ছোট্ট একটি কোণের ঘর আর লাগোয়া চালা ছাদের মতোই যেন বিস্তৃত রবির ছুটির দিন। অজানা ভিন্ দেশের ছুটি, পুরনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই মেলা ভার। বউকথা কও ডাকছে তো ডাকছেই উড়ো ভাবনায় ভেসে যাচ্ছে রবি আর সেই সাথে কবির খাতা ভরে উঠছে নতুন নতুন পদ্যের ভাবনায়। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফলনের আমের বোল - যেন ঝরে পড়ার অপেক্ষায়।
রবির কাছে জ্যোতিদাদা ছিলেন এক বিষ্ময়। তিনি ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালোবাসতেন।বউঠাকুরনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে মাঝে মাঝে তিনি চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যেতন। একবার শিলাইদহে বেড়াতে গিয়ে রবিকে দিলেন এক টাট্টুঘোড়া। সে ঘোড়া ছিল খুব দৌড়বাজ। রবিকে ঘোড়াটি দিয়ে বললেন রথতলার মাঠ থেকে দৌড় করিয়ে নিয়ে আসতে। এবড়ো খেবড়ো মাঠে শুরু হল দৌড়। পড়ি পড়ি করতে করতে রবিও ছুটলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে। জ্যোতিদাদা জানতেন যে রবির সেই সাহস আছে, অন্তত ভূ-পাতিত হবে না। কিছু কাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও রবিকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে ঘোড়া রবিকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে, যেখানে সে দানা খেত। ব্যাস, পরদিন থেকেই বাড়ির আপত্তিতে রবির ঘোড়া চড়া সাঙ্গ হল।
মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা হাওয়া বদল করতে যেতেন গঙ্গার ধারের বাগান বাড়িতে। সে ছিল এক দোতলা বাড়ি। বিলিতি সওদাগরির ছোঁয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে পড়েনি দুইধারে তার পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার কলের চিমনিগুলো তখনও ছাড়েনি তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। বর্ষা নেমেছে নতুন। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউখেলিয়ে ; মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। এরকম বহুদিনে কবি গান বেঁধেছেন - কিন্তু সেদিন তা হওয়ার ছিল না বোধহয়। কবির মনে বিদ্যাপতির একটা পদ জেগে উঠল -
"এ ভরা বাদর, মহা ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"
কবি বলেছেন - " নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিনীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাবাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে - থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি লেগে গেছে ডালে - পাতায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বউঠাকুরন এলেন, গান শোনালুম তাঁকে ; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। "
পূব দিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম সাজানো হত সকালে। সেই সময় জ্যাতিদাদা পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেওয়ার জন্য রবির ডাক পড়ত। তাঁর অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনগুলো রবি সযত্নে জুড়ে দিতেন। ক্রমে রোদের তাপ বাড়লে ছায়া যেত ক্ষয়ে, ছাদটা উঠতো তেতে।
দুপুরে জ্যোতিদাদা চলে যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বউঠাকুরন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতে তৈরি কিছু কিছু মিষ্টিও থাকত সাথে আর তার উপরে ছড়ানো হ'ত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস খোলা ছাড়িয়ে বরফে ঠাণ্ডা করা। পুরো রেকাবিটার উপর একটা ফুল কাটা রেশমের রুমাল ঢেকে সোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা - দুটোর সময় রওনা করে দিতেন । রবি ছিলেন নীরব দর্শক, সবকিছুর সাক্ষী। জ্যোতিদাদা এবং বউঠাকুরন ছিলেন তাঁর অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত নিজের । সারাদিনের সময়ের অনেকটা জড়িয়ে থাকতেন বউঠাকুরন ও জ্যোতিদাদা।
শিশুকাল থেকে রবির পরিবারে যে গানের চর্চা গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন জ্যোতিদাদা। কবির ক্ষেত্রে একটা সুবিধা ছিল এই যে অতি সহজেই গান তাঁর সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। অবশ্য তার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করেও গান আয়ত্তে আনার উপযুক্ত অভ্যাস না থাকায়, তাঁর শিক্ষা পাকা হয়নি। তাই সংগীত বিদ্যা বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে কবি কোন অধিকার লাভ করতে পারেন নি।
জ্যোতিদাদার কাছে খুব বড় রকমের স্বাধীনতা পেয়েছিলেন রবি, তাঁর সংস্রবে কবির ভিতরের সকল সংকোচ দূর হয়েছিল। এরূপ স্বাধীনতা বোধহয় কেউ তাঁকে দিতে সাহস করতেন না, সেজন্য হয়ত কেউ কেউ তাঁর নিন্দাও করেছেন। কবি লিখেছেন - "প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধা নিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনই অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে বন্ধন মুক্তি না ঘটিলে চির জীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবল পক্ষেরা সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। " আরো বলেছেন " শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই।"
জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন - ফ্লাটিলা কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে অবশেষে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে ফেললেন, কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বউঠাকুরনের। এরপর জ্যোতিদাদা তাঁর তেতলার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষ কালে আর এক বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।
কবি কৈশোর বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন তা লিখতে গিয়ে কবি নির্দয় ভাবে বললেন,
" আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে যাহা কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়া রাখে, সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেয় না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত যাইতে দেয় না, তাহাকে পুরোপুরি ছাড়িয়া দিতে চায় না ; এইজন্য সকল প্রকার আঘাত আতিশষ্য অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সঙ্গী। মঙ্গলকর্মে যখন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে তখনই তাহাদের বিকার ঘুচিয়া যায়, তখনই তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠৈ। আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে, আনন্দের পথ সেই দিকে। "
এখানে কবির যা অনুভব তা সহজ ভাষায় বললে - অন্তরে নিষ্পেষিত হওয়া যে বালক বেলার প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তিগুলোর মুক্তিতেই সহজতা, বিকার দূরীকরণ এবং স্বাভাবিকতা। অবশ্য সে মুক্তিলাভ হওয়া চাই অবশ্যই মঙ্গল কর্মে, কোনো অসৎ, কোনো পরকীয়া, কোনো নকল করা, অথবা অভিজ্ঞতাহীন শখের কাব্য চর্চার মধ্যে নয়। স্বাভাবিক মাঙ্গলিক কর্মেই বা সাধনায় সে সকল প্রবৃত্তির মুক্তি। প্রবৃত্তিগুলির মুক্তিতেই লেখা হয় আনন্দের পথ। স্বার্থসাধনের প্রক্রিয়ায় সে প্রবৃত্তি হয়ে ওঠে ভীষণ, যা মনকে অশান্ত করে, সুস্থ কাব্য চেতনার বা সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের তা অন্যতম অন্তরায়।
শূন্যতাকে মানুষ কোনও মতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারে না। যা নেই তা মিথ্যা, যা মিথ্যা তা নেই। এই জন্য যা দেখা যায় না তাকে দেখার চেষ্টা, যা পাওয়া যায় না তাকে পাবার অন্বেষণ কিছুতেই থামতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরে রাখলে তার যেমন সকল চেষ্টা থাকে সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়িয়ে আলোর পথে মাথা তুলতে, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আলোর দিকে শাখা প্রশাখাকে বিস্তৃত করে দিতে তেমনই মৃত্যু এসে যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ-ই একটা ' নেই ' - অন্ধকারের বেড়া গড়ে দেয়, তখন সমস্ত মন প্রাণ দিনরাত এক দুঃসাধ্য চেষ্টায় তারই ভিতর দিয়ে কেবলই ' আছে' - আলোকের মধ্যে প্রকাশ পেতে চায়। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তার মতো দুঃখ আর কিই - বা হতে পারে।
এর আগে রবি কোনোদিন সেভাবে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেননি। বাড়িতে ঘটে গেল পর পর কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা। অনেকদিন ধরেই রবির মা ' সারদা দেবী' রোগে ভুগছিলেন। তখন রবির বয়স মাত্র ১৪ বছর, কবি মাতৃহারা হলেন। কখন যে তাঁর জীবনসংকট শিয়রে এসে উপস্থিত হল তা কবি বুঝতেও পারেন নি।
তখন অনেক রাত্রি - একজন পুরনো দাসী রবির ঘরে ছুটে এসে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ' ওরে তোদের কি সর্বনাশ হল রে।' বউঠাকুরন তাড়াতাড়ি তাকে ভৎসনা করে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেলেন - পাছে গভীর রাত্রে আচমকা ছোটদের গুরুতর আঘাত না লাগে। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোয়, ক্ষণকালের জন্য রবি জেগে উঠে তাঁর বুকটা হঠাৎ-ই কেমন দমে গেল। কিন্তু কি হয়েছে - তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না। ভোরবেলা উঠে যখন মা'র মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তখন সে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। বাইরের বারান্দায় এসে দেখলেন - মায়ের সুসজ্জিত দেহ উঠোনে খাটের উপরে শোয়ানো রয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে দেহে তার কোনো প্রমাণ ছিল না ; সেদিন সকালের আলোতে মৃত্যুর যে রূপ দেখলেন তা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন থেকে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করে তেমনভাবে চোখে পড়ল না। কেবল যখন তাঁর দেহ সকলে বয়ে নিয়ে তাঁকে বাড়ির সদর দরজার বাইরে নিয়ে গেল এবং কবি তাঁদের পিছু পিছু শ্মশানে চললেন তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে দমকা হাওয়ার মতো এসে মনের ভিতরটাতে একটা হাহাকার রব তুলে দিল। রবি মনে মনে উপলব্ধি করলেন - এই বাড়ির এই দরজা দিয়ে মা আর এক দিনও তাঁর নিজের এই চির জীবনের ঘরকরনার মধ্যে নিজের আসনটিতে এসে বসবেন না।
কবি লিখছেন - " ইহার পর বড় হইলে যখন বসন্ত প্রভাতে একমুঠো অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি! "
মায়ের মৃত্যুর পর কিছুকাল ধরে কবির রাতে শোওয়ার জায়গা ছিল তেতলার বাইরের বারান্দা - কি শীত কি বাদল। সেখানে সারা রাত আকাশের তারাদের সাথে রবির চোখাচোখি হত, মনের আদান প্রদান হত এবং ভোরের আলোর সাথে সাক্ষাতের বিলম্ব ঘটত না। সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির কাছে যেন আরো রমনীয় হয়ে উঠছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি তাঁর অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলে গিয়েছিল বলেই, চারদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ভারী একটি মাধুরী বর্ষণ করত। জগতকে সম্পূর্ণ করে এবং সুন্দর করে দেখবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটিয়ে দিয়েছিল। কবি নির্লিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং জেনেছিলেন যে তা বড়ই মনোহর।
বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যু রাজ্যের কোনো একটা চূড়ার উপরের একটা ধ্বজাপতাকা তার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখবার জন্য কবি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলিয়ে ফিরতেন। সকালবেলায় যখন বাইরের পাতা বিছানার উপর ভোরের আলো এসে পড়ত তখন কবি চোখ মেলে দেখতেন, তাঁর মনের সকল আবরণ যেন স্বচ্ছ হয়ে আসছে, কুয়াশা কেটে গেলে পৃথিবীর নদনদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করে ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি তাঁর চোখে তেমনি শিশিরে সিক্ত নবীন ও সুন্দর হয়ে যেন দেখা দিচ্ছে ক্রমান্বয়ে।
- - - সমাপ্ত - - -
#অরিজিৎ #রায়
তথ্যসূত্র :
১. বিচিত্রা রবি ঠাকুর
২. জীবনস্মৃতি রবি ঠাকুর
৩. ছিন্নপত্রাবলী রবি ঠাকুর
৪. ছেলেবেলা রবি ঠাকুর
৫. রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম,
১১তম এবং ১২ তম খণ্ড
৬. পিতৃস্মৃতি রবি ঠাকুর
৭. শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন
(গোপাল হালদার সম্পাদিত)
ক) রবীন্দ্র নাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক -
সরোজ বন্দোপাধ্যায়
খ) রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা
গোপাল হালদার
৮. ভানুসিংহ ঠাকুর ও টমাস চ্যাটার্টন - প্রবন্ধ
৯. আন্তর্জাল











































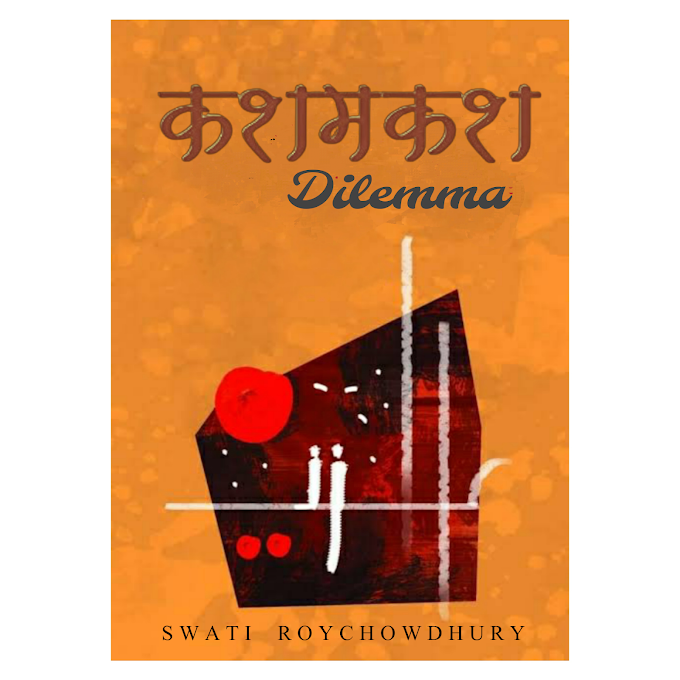



0 মন্তব্যসমূহ